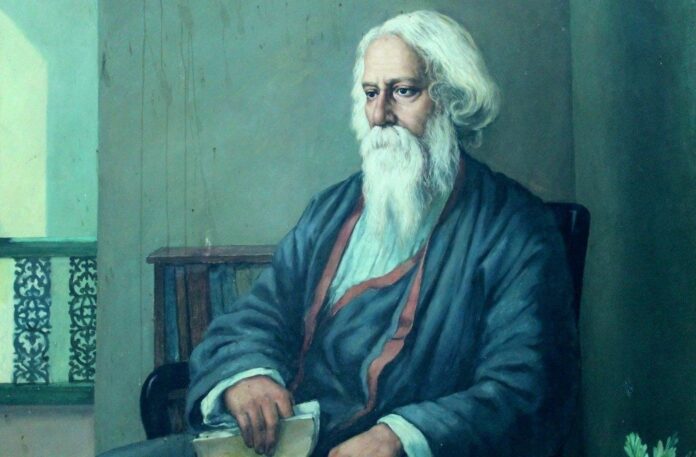রবীন্দ্রনাথ নিজেই কিন্তু এই তথাকথিত রাবীন্দ্রিকতার সংজ্ঞা মেনে চলেননি সবসময়, অন্তত ভাষার ক্ষেত্রে। আর এটি সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় তাঁর গানের বাণীতে। বর্তমান নিবন্ধটি এমন কৌতূহলোদ্দীপক একটি বিষয়ের ওপরই কিঞ্চিৎ আলোকপাতের একটি প্রাথমিক প্রয়াসমাত্র।
আলম খোরশেদ:
বাংলা ভাষায় রাবীন্দ্রিক এবং তার বিপরীতে অরাবীন্দ্রিক শব্দদুটোর বহুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এতটাই যে, এই রাবীন্দ্রিক শব্দটির একটি সংজ্ঞার্থই প্রায় দাঁড়িয়ে গেছে। ফলত শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গেসঙ্গে আমাদের মানসলোকে একটি শুদ্ধ, শালীন, প্রমিত, পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত ছবি ভেসে ওঠে। অথচ মজার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই কিন্তু এই তথাকথিত রাবীন্দ্রিকতার সংজ্ঞা মেনে চলেননি সবসময়, অন্তত ভাষার ক্ষেত্রে। আর এটি সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় তাঁর গানের বাণীতে। বর্তমান নিবন্ধটি এমন কৌতূহলোদ্দীপক একটি বিষয়ের ওপরই কিঞ্চিৎ আলোকপাতের একটি প্রাথমিক প্রয়াসমাত্র। এই উদ্দেশ্যে আমি তাঁর সুবিখ্যাত গানের সংকলন গীতবিতান এর পূজা, প্রেম ও প্রকৃতি পর্ব থেকে বেশ কিছু শব্দ, শব্দবন্ধ ও বাক্যাংশের উল্লেখ করব এখানে, যা আমার এহেন মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণে সহায়ক হবে বলে মনে করি।
পূজাপর্বের একেবারে প্রথম গান কান্নাহাসির দোল-দোলানোতেই আমরা একটি অপ্রচলিত শব্দ, আলার দেখা পেয়ে যাই, যেটিকে আমরা পরে তাঁর আরও কটি গানে, যেমন বলি ও আমার গোলাপবালা, আমার অভিমানের বদলে ইত্যাদিতেও দেখতে পাব। আলোকিত, উদ্ভাসিত অর্থে এই শব্দটির এমন প্রয়োগ সচরাচর দেখা যায় না বললেই চলে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এর প্রয়োগে কুণ্ঠিত ছিলেন না মোটেও। এর কয়েকটি গান পরেই ঝরনাতলার নির্জনে আমরা একখানি কলস এর সন্ধান পাই, যে-শব্দটিকেও ঠিক রাবীন্দ্রিক আখ্যা দেবেন না কেউ, কিন্তু এই নিতান্ত আটপৌরে শব্দটিকেই রবীন্দ্রনাথ ঘুরেফিরে ব্যবহার করেছেন তাঁর আরও অনেক গানে। তেমনি আরেকটি অত্যন্ত ঘরোয়া, সাংসারিক শব্দ ঢাকনা খুলে যেতে দেখি আমরা তাঁর বহুলপরিচিত গান এমনি করে যায় যদি দিন যাক নায়।
গোটা বাংলাগানের ইতিহাসে আর কোথাও কখনও এহেন এক অরাবীন্দ্রিক শব্দের এমন মোক্ষম প্রয়োগ হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। এই পূজাপর্যায়েরই অসীম ধন তো আছে তোমার গানের দ্বিতীয় চরণেই দেখি তিনি বণ্টন অর্থে অবলীলায় ব্যবহার করেন আরেকটি গার্হস্থ্য শব্দ: বেঁটে। তেমনি, শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে গানটির একেবারে শেষ দিকে ব্যবহৃত ভুখের পরের মতো শব্দবন্ধ প্রয়োগ করতেও বুকের পাটা লাগে বই কি!
আমরা অনেকেই যথাযথ পটভূমিটুকু না জেনেই পূর্ণিমাকালে আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে গানটি গাইতে খুব পছন্দ করি, কিন্তু কজনে খেয়াল করি যে এই গানে রবীন্দ্রনাথ ধুতে হবে, মুছতে হবের মতো দুটো প্রাত্যহিক গেরস্থালিকর্মকে কী এক অসামান্য উচ্চতায় নিয়ে যান! ক্ষালন ও প্রক্ষালনের বিষয়টি অবশ্য তাঁর গানে ফিরে ফিরেই এসেছে; যেমন এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, আজ আলোকের এই ঝর্নাধারায় ধুইয়ে দাও, তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে গানদুটির কথা। দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে গানটির কথা ভাবলেই একধরনের ভক্তি ও সম্ভ্রমের উদয় হয় আমাদের মনে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার বিন্দুমাত্র ধার না ধেরে তথাকথিত সুশীল শব্দ মুঠোর বদলে তোমার মুঠা কেন ভরিনের মতো লাইন লিখতেও দ্বিধা করেননি এতে। ঠিক একইভাবে নয় এ মধুর খেলার মতো সুমধুর এক সংগীতে তিনি আচমকা কী দারুণ ধাক্কাই না মারেন আমাদের, সংসারের এই দোলায় দিলে সংশয়েরই ঠেলা দিয়ে। তেমনি তুলনামূলকভাবে একটু কম পরিচিত গান তুই কেবল থাকিস সরে সরে-তে ঠাকুর প্রমিত ক্রিয়াপদ এগিয়ের পরিবর্তে অপ্রচলিত আগিয়ে ব্যবহারেও পিছপা হন না।
একইভাবে, আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায় গানে আর্ত না লিখে আতুর আর দৃষ্টির পরিবর্তে দিঠি লিখতে তাঁর কোনো সংকোচই হয়নি। এরকম উদাহরণ আরও রয়েছে। যেমন, দুখেরে করি না ডর (পুষ্পবনে পুষ্প নাহি), পুজার থাল রে (ওরে কি শুনেছিস ঘুমের ঘোরে), সবাই তোমায় তাই পুছে (কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও), আঘাত করে নিলে জিনে ইত্যাদি। নিবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করা আলার মতোই আরেকটি দারুণ মৌলিক ও বুদ্ধিদীপ্ত শব্দপ্রয়োগ আমরা লক্ষ করি তাঁর অকারণে অকালে মোর পড়ল যখন ডাক গানের এই —-আশ্রিত পংক্তিটিতে: আধেক দেখা করে আমায় আঁধা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলোতে এজাতীয় সাধু, কথ্য, আঞ্চলিক ও আটপৌরে শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি একদমই অচেনা, অচলিত শব্দপ্রয়োগেও সমান নিঃশঙ্ক ছিলেন।